উৎসব সংখ্যা প্রবন্ধ: বাংলা সিনেমায় কমেডি অভিনয় ও অভিনেতারা
বাঙালির জীবন থেকে নির্মল হাসি কবেই চলে গেছে। একটা সময় ছিল যখন চলচ্চিত্র, নাটক, রেডিও, কিংবা সাহিত্যে হাস্য-কৌতুকের উপস্থিতি ছিল মর্যাদাময়। গানের জলসাতে হাস্য-কৌতুকের অনুষ্ঠান থাকতোই। এমনকি কাজের বাড়িতে গানের সঙ্গে নবদ্বীপ হালদার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়দের কৌতুক নকশার রেকর্ড বাজতো। অনেক কিছুর মতই বাঙালির সমাজজীবন থেকে নির্মল হাস্যকৌতুকও হারিয়ে গেছে। বাংলা চলচ্চিত্র ও পেশাদারী মঞ্চের নাটকে নবদ্বীপ হালদার, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়,অজিত চট্টোপাধ্যায়, অনুপ কুমার, জহর রায়, রবি ঘোষ, সন্তোষ দত্ত প্রমুখ – এক দীর্ঘ তালিকা আর হাসির গানে রঞ্জিৎ রায়, মিন্টু দাসগুপ্ত, দীপেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কত নাম বাংলার সংস্কৃতি জগতে উজ্বল হয়ে আছে।
এখন বাংলা সিনেমায় কৌতুক অভিনয় থাকে না, হাসির সিনেমা তো দূরের কথা। কারণ সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্রে পরিচালকদের আগ্রহ কমেছে। পঞ্চাশ থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত বাংলা সিনেমায় কৌতুকাভিনেতারা সিনেমার প্রযোজক-পরিচালকদের কাছে অভিনয়ের জন্য অর্থ না পান গুরুত্ব পেতেন আর সিনেমার দর্শকরা পেতেন নির্মল আনন্দ। গত শতকের পঞ্চাশ থেকে আশির দশক এই সময়কালকে বলি বাংলা ছায়াছবির স্বর্ণযুগ। তখনকার সিনেমার নির্মাণে পরিচালকদের একটা রসায়ন ছিল বাঙালির আটপৌরে জীবনের হাসিকান্নার গল্প, ভালো অভিনয়, আর মন আন্দোলিত করা সঙ্গীত। ‘ভালো অভিনয়’এই ধারণার মধ্যে কৌতুকাভিনয়ও ধরতে হবে। কান্না ও কান্নায় চাপা পড়া হাসি ভিন্ন জীবনই অসম্পূর্ণ। কৌতুক অভিনয় করেই চার্লি চ্যাপলিন বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা । তাঁর সিনেমা শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদী সিনেমাও।
বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের পিতৃপুরুষের মর্যাদা পান ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (বা ডি জি)। বাংলা ছায়াছবির পথচলা শুরু হয় ১৯১৯এর ১৯শে নভেম্বর কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে (পরে যেটির নাম হয়েছিল ‘শ্রী’) ‘বিল্বমঙ্গল’ ছবির মুক্তির মধ্য দিয়ে। বিল্বমঙ্গলের নির্মাতা ছিল ম্যাডান কোম্পানী, পরিচালক রুস্তমজি ধোতিওয়ালা আর অভিনেতৃরা ছিলেন এংলোইন্ডিয়ান (নির্বাক চলচ্চিত্র যুগে এংলো ইনডিয়ানরা নায়িকার ভূমিকায় থাকতেন)। এর দু বছর পরে ধীরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে নির্মিত হল কমেডি ছবি ‘বিলাৎ ফেরত’ মুখ্য ভূমিকায় ধীরেন্দ্রনাথ। সেদিনের ইংরাজি নবিশ বাঙালি বাবুদের দেশীয় মানুষদের প্রতি ঘৃণা ও ইংরাজ প্রীতির প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ ছিল এ ছবির কাহিনীসার। চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয় ধারা অনুসরণ করতেন ধীরেন্দ্র নাথ। অর্থাৎ আমরা দেখলাম সম্পূর্ণ বাঙালি উদ্যোগে নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্রটিই ছিল কৌতুক-ব্যঙ্গরসাত্মক সিনেমা। বাংলা সিনেমা কথা বলতে শুরু করলো ১৯৩১এ অর্থাৎ স্ববাক হল। প্রমথেশ বড়ুয়া ১৯৩৯এ নির্মাণ করলেন একটি কমেডি ছবি ‘রজত জয়ন্তী’। চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞরা বলেন, স্বাধীনতার পূর্বে বড়ুয়ার ‘রজতজয়ন্তী’ ছিল সেরা কমেডি ছবি। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের পিতৃপুরুষের মর্যাদা পান ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী বা ডিজি। বাংলা চলচ্চিত্রে হাস্যরসাত্মক অভিনয়ের পিতৃপুরুষও এই ডিজি।

দেবকী কুমার বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া,এক ঝাঁক পরিচালক ও অভিনেতাকে হাত ধরে বাংলা চলচ্চত্রি শিল্পে নিয়ে এসেছিলেন তারমধ্যে কজন ছিলেন অনন্য কৌতুক অভিনেতা নবদ্বীপ হালদার। ১৯৩০এ পঞ্চশর ছবিতে প্রথম আত্মপ্রকাশের পর শতধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন নবদ্বীপ । ভাঙ্গা কন্ঠস্বরে কথার মারপ্যাচ ঘেরা ব্যাঙ্গাত্মক অভিনয়ের এক অনন্য ধারা তৈরি করেছিলেন নবদ্বীপ। সিনেমায় শতশত অভিনেতা কন্ঠস্বরের কলরোলে যে অভিনেতার কন্ঠস্বর আলাদা করে চিনতে কোন সমস্যা হয় না তিনি নবদ্বীপ হালদার।
চল্লিশের দশকটা বাংলার সমাজ জীবনে সুখের সময় ছিল না। ১৯৪৩এর মন্বন্তরে মৃত্যুর হাহাকার, ‘৪৬এর ভাতৃঘাতি দাঙ্গা আর ১৯৪৭এ দেশভাগ, ভিটেহারা উদ্বাস্তু স্রোত, সিনেমার পক্ষে অনুকুল সময় ছিল না। বাংলা ছবির বাজার দুই তৃতীয়াংশ সঙ্কুচিত হয়ে গেলো দেশভাগের ফলে। তবুও ‘কত ভঙ্গ বঙ্গদেশে তবু রঙ্গে ভরা’। নবদ্বীপ হালদারের পরে বাংলা চলচ্চিত্র ১৯৩০ থেকে ১৯৫০/৫২র মধ্যে উঠে এসেছিলেন আরো এক ঝাঁক কৌতুকাভিনেতা–তুলসী চক্রবর্ত (১৯৩২) অজিত চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৪), শ্যামলাহা (১৯৩৫), নৃপতি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৭), হরিধন মুখোপাধ্যায় (১৯৪৬), অনুপকুমার (১০৪৬), জহর রায় (১৯৪৭), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৮), প্রমুখ। এঁরাই পরবর্তী ত্রিশ বছর বাংলা চলচ্চিত্রে হাসির অভিনয় করে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। এদের কিছু পরে উঠে আসেন সন্তোষ দত্ত (১৯৪৮), রবি ঘোষ (১৯৫৯), চিন্ময় রায় প্রমুখ।

১৯৫১তে মুক্তি পেল রস-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে সম্পূর্ণ হাসির ছবি ‘বরযাত্রী’। এটিই সম্ভবত স্বাধীনতার পরে নির্মিত প্রথম হাসির সিনেমা। অভিনয় করেছিলেন কালি বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, জহর রায় প্রমুখ,। ‘বরযাত্রী’র পর ১৯৫৩তে পেলাম হাসির ছবি ‘সাড়ে চুয়াত্তর’। বলা যায় সাড়ে চুয়াত্তর বাংলা কমেডি ছবির ধারা নির্দেশ করে দিল। এই ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সংলাপ ‘মাসিমা মালপো খামু’ প্রবাদের মত হয়ে গেল। তারপর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে অনেক কমেডি ছবি নির্মিত হল । ‘পাশের বাড়ি’ (১৯৫২), ‘ওরা থাকে ওধারে’ (১৯৫৪), ‘টনসিল’(১৯৫৬), ভানু পেল লটারি’ (১৯৫৮), ‘যমালয়ে জীবন্ত মানুষ’ (১৯৫৮) ‘পার্সোনাল এসিসট্যান্ট’ (১০৫৯), ভ্রান্তি বিলাস’ (১৯৬৩), ভানু গোয়েন্দা জহর এসিসট্যান্ট (১৯৭১)। তখন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়া কমেডি ছবি বা সাধারণ সিনেমায় কমেডি অভিনয় ভাবা যেতো না। এমনই অপরিহার্য ছিলেন বাংলা সিনেমার সেরা কমেডিয়ান ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ।
আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা সিনেমায় কমেডি অভিনয়ে এক শূন্যতা এল । তুলসী চক্রবর্তী চলে গেছেন অনেক আগেই, ডিসেম্বর ১৯৬১তে, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় মে ১৯৭৫এ, জহর রায় অগস্ট ৭৭এ। একএকে চলে গেলেন অনুপকুমার (সেপ্টেম্বর ৮৮), সন্তোষ দত্ত (ফেব্রুয়ারি ৮৮) আর রবি ঘোষ (ফেব্রুয়ারি ৯৭)। নব্বইএর শেষ পৌঁছে বাংলা সিনেমা হয়ে পড়লো কমেডি অভিনয় হীন। নবীন অভিনেতা অনেক এলেন বটে কিন্তু তারা কেউই ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, রবি ঘোষ, সন্তোষ দত্তদের উচ্চতা ছুঁতে পারলেন না। আমরা জানি কমেডিয়ানরা শুধুমাত্র কৌতুকাভিনেতা নন, ভালো অভিনেতা। আর কে না জানি যে বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ানও বটে। বাংলা সিনেমার ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, অনুপকুমার, রবি ঘোষ, সন্তোষ দত্তরা কমেডিয়ান হয়েও উচ্চমানের চরিত্রাভিনেতার মর্যাদা পেয়েছেন।
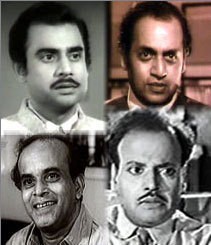
পঞ্চাশের দশকে পূর্ববঙ্গ থেকে ভিটামাটি ছেড়ে আসা বাঙালিরা কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে খুব অভিপ্রেত ছিলেন না তাদের ভাষাকে ভাঁড়ামির উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হত গল্প, উপন্যাস, থিয়েটা্র সিনেমায়। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে বাংলা সিনেমায় কমেডি অভিনয়ে এক নতুন মাত্রা নিয়ে এলেন, সৃষ্টি করলেন কমেডি অভিনয়ের একটা টাইপ। অথচ এই টাইপের বাইরে গিয়ে অসামান্য অভিনয় করেছিলেন ‘জমালয়ে জীবন্ত মানুষ’ ‘ভানু গোযেন্দা জহর এসিসট্যান্ট’, ‘ভ্রান্তি বিলাস’, ‘পার্সোনাল এসিসট্যান্ট’ ছায়াছবিতে। কমেডি অভিনয়ে ভানু যে টাইপ সৃষ্টি করেছিলেন সেটি পরবর্তীকালে আর কেউ ছুঁতে পারলেন না। সিনেমা থিয়েটারের কমেডিয়ানদের একটা বেদনা, একটা উপেক্ষার যন্ত্রণা বয়ে বেড়াতে হয় সারা জীবন। অনাবিল হাসি বিলোচ্ছেন যারা সেই আনন্দের পেছনে তাদের চাপা কান্নার কথা তাঁরা দর্শকরা বুঝতে পারেন না। সে সব কান্নার কিছু বৃত্তান্ত রাজ কাপুরের ‘মেরা নাম জোকার’ কিংবা গৌতম ঘোষের ‘বাঘ বাহাদুর’ ছবিতে দেখেছি । কমেডিয়ানের জীবনের বেদনা নিয়ে ভানু ব্যানার্জীকে প্রধান চরিত্রে নিয়ে একটি ছবি হয়েছিল ‘নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে’। সিনেমায় আসার আগে ভানু থিয়েটারে চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চানক্যের মত কঠিন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। অথচ সিনেমায় তিনি কমেডিয়ান হয়েই রইলেন । চরিত্রাভিনেতা হিসাবে তাঁর মূল্যায়ন হয়নি। সত্যজিৎ রায় ‘পরশ পাথর’ সিনেমায় তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয় প্রতিভার ব্যবহার করেছিলেন, ‘পলাতক’ ছবিতে তরুণ মজুমদার অনুপকুমারের অবিস্মরণীয় অভিনয় প্রতিভার মর্যাদা দিয়েছিলেন তাঁকে প্রধান চরিত্রে নির্বাচিত করে । ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটুকুই প্রাপ্তি যে তিনি বাংলা সিনেমায় এতাবৎ কালের সেরা কমেডিয়ান। চলচ্চিত্র ইতিহাসবিদ ও গবেষক স্বপন কুমার ঘোষের একটা লেখা থেকে উধৃতি দিই – “ ‘লাইমলাইট’ দেখে বাড়িতে এসে কেঁদেছিলেন ভানুদা। স্বগতোক্তির মতো করে সেদিন তাঁর স্বজনদের তিনি বলেছিলেন, ‘‘মইর্যা গেলেও লোকে বিশ্বাস করব না, কইব আমি হ্যালারে হাসাইতাছি। আমাগো দেশে এইটাই ট্র্যাজেডি, কমেডিয়ানরে লোকে ভাঁড় ভাবে”। কৈশোরে স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া শহিদ বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তর বাল্যবন্ধূ ভানু (প্রকৃত নাম সাম্যময়) তাঁর ৩৭ বছরের সিনেমা জীবনে অভিনয় করেছেন ২৩৫টি চলচ্চিত্রে। তাঁর নিজের কথায় ‘‘বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যা কিছু সমাজের, সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী, আমি দরকার মতো, সাধ্য মতো তার বিরুদ্ধে মানুষকে খোঁচা দিয়ে জাগানোর জন্য নাটক, সিনেমা করে যেতে চাই— তা সে ব্যঙ্গ বা সিরিয়াস, যা কিছু হোক না কেন। এটাই আমার কমিটমেন্টের শেষ কথা”।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা এলেই অবধারিতভাবে এসে যায় জহর রায়ের কথা, দুজনে যেন মাণিকজোড়, একই ব্রাকেটে দুটি নাম ভানু-জহর। চার্লি চ্যাপলিনকে গুরু মেনেছিলেন ভানুর চেয়ে এক বছর আগে সিনেমায় আসা জহর রায়। ভানুর প্রথম ছবি ১৯৪৭এ আর জহরের ১৯৪৬এ। ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেন তিন কৃতি চিত্র পরিচালকের ছবিতেই জহর অভিনয় করেছেন। কমেডি অভিনয়ে জহর রাহের প্রধান অস্ত্র ছিল শরীরি অভিনয়। চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার মত প্রকাশ করেছিলেন “ওঁর গায়ে কমেডিয়ানের তকমা জুড়ে দেওয়া অনুচিত।’’ ঋত্বিক ঘটকের সূবর্ণরেখায় ফোরম্যান মুখার্জী, সত্যজিতের হাল্লারাজার মন্ত্রী, তরুণ মজুমদারের ‘পলাতকএ সেই যাত্রাপাগল কবিরাজ চরিত্রাভিনেতা হিসাবে ভোলা যায় না জহর রায় কে। থিয়েটারেও তিনি অভিনয় দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। কলকাতার রংমহল থিয়েটার যখন মালিক বন্ধ করে দিয়েছিল তখন তিনি উদ্যোগ নিয়ে রঙমহল শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে থিয়েটার চালিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু কমেডিতে আটকে না থেকে সিনেমায় এবং থিয়েটারেও নতুন নতুন চরিত্রে রূপায়ন করতেন শক্তিশালী চরিত্রাভিনেতা জহর রায়। তবু জহর রায়ের গায়ে কমেডিয়ানের তকমাই লেগে আছে। কোন অভিনেতাই নিজের গায়ে লেগে থাকা কমেডিয়ানের তকমা ভাংতে পারেন না, জহর রায়ও পারেননি। ‘দেহপট সনে নট সকলি হারায়’ ১৯৭৪এ শরীর ভাংতে শুরু করল। অমন গোলগাল শরীর ভেঙে যেন কঙ্কাল। সিনেমায় কাজ পাওয়া বন্ধ হল। ১৯৭৭এর ১১ই অগস্ট, ৩২ বছর ধরে সিনেমা-থিয়েটারের দর্শককে নির্মল আনন্দ বিলানো জহর রায়ের মৃতদেহের পাশে শুধু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় আর পাড়ার কিছু ছেলে। ভেঙ্গে পড়ে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন ‘জহরের কি দেশের কাছে এইটুকুই পাওনা ছিল সৌমিত্র? অন্য দেশ হলে স্যার উপাধি পেত।’ ভানু-জহর ব্রাকেট ভেঙে জহর চলে গেলেন , ব্রাকেটের অপর জন ভানু গেলেন আরো ছ বছর পরে।
বাংলা সিনেমা কথা বলতে শুরু করেছিল অর্থাৎ স্ববাক হয়েছিল ১৯৩১এ । ১৯৩২এও ১০টি নির্বাক ছবি নির্মিত হয়েছিল। ১৮৩৩এ একটিও নয় অর্থাৎ ১৯৩৩ থেকে পুরোপুরি স্ববাক চলচ্চিত্রের যুগ। বাংলা সিনেমার আদিপর্বে বা প্রথম দশকে কমেডিয়ান বলতে ছিলেন তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হালদার, শ্যাম লাহা আর নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। হলিউডি কমেডি জুটির অনুকরণে বাংলা সিনেমাতেও নবদ্বীপ হালদার- শ্যাম লাহা জুটি বেঁধেছিলেন। দুজনকে নিয়ে ‘মাণিকজোড়’ নামে একটা সিনেমাও হয়েছিল। শ্যাম লাহা গান গাইতে পারতেন, পারতেন তবলা বাজাতে। লখনৌতে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে পাহড়ি সান্যালের গানের সঙ্গে তবলা বাজিয়েছিলেন। পাহাড়ি সান্যাল শ্যামকে সিনেমায় নামতে বলেন এবং প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। বাংলা সিনেমায় শ্যাম লাহা এলেন ১৯৩৪এ । হিন্দিতে কথা বলতে জানা ও চেহারার গুনে বোকা বোকা অবাঙালি চরিত্র, মারোয়ারি ব্যবসায়ী, বড়বাজারের গদির মালিক ইত্যাদি চরিত্রে অভিনয় করার জন্য শ্যাম লাহার ডাক পড়তো। নবদ্বীপ হালদারের প্রসিদ্ধি ছিলবিকৃত কন্ঠস্বর ও গ্রাম্য ভাষায় সংলাপ উচ্চারণ। গ্রামফোন রেকর্ডে দুজনের বেশ কয়েকটি কৌতুক নক্সা তখন জনপ্রিয় হয়েছিল।
খুবই শক্তিশালী অভিনেতা ছিলেন নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। লোক হাসানোর জন্য কোন রকম ভাঁড়ামির আশ্রয় নিতেন না। অঙ্গভঙ্গি ও বাচনভঙ্গিতে এক স্বাতন্ত্রতা নিয়ে এসেছিলেন তিনি। ১৯৩৬এ প্রথম ছবি ‘দ্বীপান্তর’ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছিলেন অকৃতদার নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। কোন বড় বা প্রচারের আলো পড়ার মত চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ তিনি পাননি তাঁর প্রায় চল্লিশ বছরের সিনেমা জীবনে, তবু যেটুকু সুযোগ পেয়েছিলেন তাতেই তিনি বাংলা সিনিমার কমেডি অভিনয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন। নির্জন সৈকতে সিনেমায় এক দরিদ্র পুরোহিত চরিত্রটির কথা, কিংবা কাবুলিওয়ালা চিত্রে কয়েদি চরিত্রের কথা অনেকেরই মনে থাকবে। কিংবা গুপীগায়েন-বাঘা বায়েন চিত্রে হাল্লা রাজার বোবা প্রহরীর কথা। অথচ অভিনয়ের জন্য কোনদিন কোন পুরস্কার পাননি সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ,তরুণ মজুমদার সহ বিভিন্ন পরচালকের প্রায় ৪৫০ চলচ্চিত্রের অভিনেতা নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। দারিদ্র ও নিঃসঙ্গতামাখা শেষ দিনগুলোতেও এ-নিয়ে তাঁর কোন আক্ষেপ ছিল না। বরং বলতেন, “সবাই কষ্টের মধ্যে থাকে, হাসবে কি করে? আমি সেই বিষণ্ণ মুখে হাসি ফোটাই-এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি থাকতে পারে?”

১৯৪৩এ সিনেমায় এলেন হরিধন মুখোপাধ্যায়। তার বছর পাঁচেক আগেই নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির দলে নাট্যাভিনয় শুরু করেছিলেন। বিচিত্র জীবন ছিল তাঁর। হাতিবাগান বাজারে আলু বিক্রি করেছেন, মনিহারি দোকান দিয়েছেন, স্যার আশুতোষ আর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে গান শুনিয়েছেন। এহেন হরিধন বাংলা সিনেমায় কমেডি অভিনয়ে যেন নতুন সংজ্ঞা নির্দেশ করে দিলেন। ছন্দময় সংলাপ উচ্চারণ ও বাচিক অভিনয়ে একটা নিজস্বতা বজায় রাখতেন তিনি।
শক্তিশালী অভিনেতা অনুপকুমারের গায়েও কমেডিয়ানের তকমা লেগে আছে । অথচ কমেডি অভিনয়ের বাইরেও নায়ক ও খল চরিত্রেও সফল তিনি। তরুণ মজুমদারের ‘পলাতক’ (১৯৬৩)এ নায়কের ভূমিকায় অনুপের অবিস্মরণীয় অভিনয় তাঁকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান এনে দিয়েছিল। ১৯৬৫তে তরুণ মজুমদারের ‘আলোর পিপাসা’ ছবিতে তাকে খলচরিত্রে অভিনয় করতে দেখেছি। ১৯৩৮এ মাত্র ৮ বছর বয়সে শিশুশিল্পী রূপে বাংলা সিনেমায় এসেছিলেন অনুপ। তারপর ১৯৯৭এ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ৩৫০ ছবিতে অভিনয় করেছেন।
১৯৫৩র সিনেমা ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ বাংলা কমেডি সিনেমার একটা মাইলফলক হয়ে আছে। উত্তমকুমার – সুচিত্রা সেনের রোমান্টিক জুটির নির্মাণ এই ছবিতেই হয়েছিল। এই জন্য নয়, সাড়ে চুয়াত্তরকে মাইল ফলক বলবো এই জন্য যে এই ছবি থেকেই বাংলা চলচ্চিত্রে কমেডি সিনেমা সিনেমা নির্মাণের এক দিকনির্দেশ হয়ে আছে। তখনকার বাংলা সিনেমার প্রায় কমেডি অভিনেতার সমাবেশ ঘটেছিল এই ছবিতে। তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়– কে ছিলেন না এ ছবিতে! আর একটা কথাও মনে রাখা দরকার যে, স্ববাক বাংলা সিনেমার বয়স তখন মাত্র কুড়ি বছর । এবং এই শিল্পীরাই পরবর্তী ত্রিশ বছর বাংলা সিনেমায় কমেডি অভিনয়ের চাহিদা মিটিয়েছেন এবং কমেডি অভিনয়ের দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করেছেন।

১৯৫৩র সাড়ে চুয়াত্তরের পরবর্তী কালে বাংলা সিনেমা পেয়েছিল তিন শক্তিমান কমেডি অভিনেতাকে, তাঁরা হলেন রবি ঘোষ, সন্তোষ দত্ত ও চিন্ময় রায়। সিনেমায় আসার আগে রবি ঘোষ ছিলেন উৎপল দত্তর লিটল থিয়েটার গ্রুপে। ১৯৫৮এ উৎপল দত্তর ‘অঙ্গার’ নাটকে তাঁর অবিনয় সাফল্য রবি ঘোষকে সিনেমায় টেনে আনে। সিনেমায় প্রথম অভিনয় ১৯৫৯এ। তারপর ১৮৬২তে সত্যজিৎ রায়ের ‘অভিযান’এর পর তপন সিংহর ‘গল্পহলেও সত্যি’ তে অবিস্মরণীয় অভিনয়। এবং ১৯৬৮তে ‘গুগাবাবা’। প্রায় ২০০বাংলা সিনেমায় রবি ঘোষের উজ্বল উপস্থিতি। রবি ঘোষ বাংলা সিনেমায় কমেডি অভিনয়ে এক মার্জিত ধারা নিয়ে এলেন, যা তাঁর নিজস্ব, দর্শককে জোর করে হাসানোর কোন চেষ্টা করতেন না । রবির অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য তাঁর সংলাপ বলার টাইমিং এবং মুহুর্তে মুখের ভাব পরিবর্তন । রবি ঘোষের অভিনয় প্রসঙ্গে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও উৎপল দত্তর মন্তব্য স্মরণযোগ্য। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন –“রবি বড় মাপের অভিনেতা ছিল বলেই বড় মাপের কৌতুকাভিনেতা হতে পেরেছিল… যিনি বিশ্বের সেরা অভিনেতা তিনিই বিশ্বের সেরা কৌতুকাভিনেতা – চার্লস চ্যাপলিন”। আর উৎপল দত্ত লিখেছেন… “এন্ড হি হ্যাস নাউ বিকাম হোয়াট হি ওয়ান্টেড টু বি, পারহ্যাপস দি সুপ্রিম কমেডিয়ান ইন আওয়ার সিনেমা … হি ইস পারহ্যাপস দি বেস্ট অ্যাক্টর আই হ্যাভ এভার হ্যাড দি অনার টু ওয়ার্ক উইথ”। রবি ঘোষের বন্ধু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন “ক্ষণজন্মা তুলসী চক্রবর্তী এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায়ের মত অসামান্য অভিনয়ের মধ্য দিয়েবাংলা ছবিতে কমেডি অভিনয়ের একটা উচু মান প্রবাহিত হয়ে এসেছে। রবি এই মহান ঐতিহ্যের শেষ প্রতিনিধি বএ আমি মনে করি পূর্বসুরীদের মত তার অভিনয়েও গভীর ও তীব্র জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়…। জীবনের ও মানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রবি যেভাবে কাজে লাগিয়েছে তার জন্য”। বাংলা সিনেমায় কমেডি অভিনয়ে ভানু-জহর –রবি ঘোষদের দাপটের কালেই এসেছিলেন চিন্ময় রায়, দর্শক যাকে মনে রেখেছেন টেনিদার চরিত্র সৃষ্টির জন্য। তারপর বাংলা সিনেমায় তেমন কমেডি চরিত্রই সৃষ্টি হল কোথায় আর তেমন কৌতুকাভিনেতাই বা কোথায়? কাঞ্চন বা শুভাশিষ মুখার্জীরা হরিধন-ভানু-জহরদের সঙ্গে কোন তুলনাতেই আসেন না। বরং খরাজ মুখার্জী, পরান বন্দ্যোপাধ্যায় কমেডি অভিনয়ের দাবি কিছুটা মেটানোর ক্ষমতা রাখেন।
সিনেমার নায়ক নায়িকার মতই কমেডিয়ানরাও তাদের সৃষ্ট চরিত্রের জন্য দর্শক মনে স্মরণীয় হয়ে থাকেন বহুদিন। তুলসী চক্রবর্তীর পরেশ বাবু (পরশ পাথর), জহর রায়ের হল্লা রাজা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রান্তি বিলাস, অনুপ কুমারের আংটি চাটুজ্জের ভাই, রবি ঘোষের বাঘা ও গল্প হলেও সত্যির রাধুনী, চিন্ময় রায়ের ননী গোপাল ও টেনিদা চরিত্রগুলি স্মরণীয় হয়ে আছে। সেইরকমই লালমোহন বা জটায়ুর চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সন্তোষ দত্তও স্মরনীয় হয়ে আছেন। তার মৃত্যুর পর অনুপ কুমার, রবি ঘোষ ও বিভু ভট্টাচার্য জটায়ুর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কিন্তু এদের কেউই সন্তোষ দত্তর অভিনয়কে ছুঁতে পারেননি। পেশায় আইনজীবি সন্তোষ দত্ত খুব বেশি সংখ্যক সিনেমায় অভিনয় করেননি। তার ছবির সংখ্যা পঞ্চাশেরও কম। তারই মধ্যে বাংলা সিনেমায় কমেডি অভিনয়কে এক অভিজাত উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। শিশুসুলভ অপাপবিদ্ধ মুখভঙ্গি তাঁরকথা বলা চোখের ভাষা ছিল তার অভিনয়ের সম্পদ।

বাংলা সিনেমার জন্মলগ্ন থেকে প্রায় সব সার্থক কমেডিয়ানদের ছুঁয়ে গেলাম, কিন্তু একজনের কথা এখনও বলিনি। আসলে তাঁকে আর কারো সঙ্গে মেলানো যায় না, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, অনন্য তুলসী চক্রবর্তী। বাংলা সিনেমার নিতান্ত শৈশবে তিনি এসেছিলেন (১৯৩২–পুনর্জন্ম ছবিতে)। এর অনেক আগেই সবে কৈশোর পেরনো তুলসী থিয়েটারে এসেছিলেন জ্যাঠামশাইএর হাত ধরে তবলা বাদক হিসাবে, এবং পরে অভিনয়ে। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জিত ছিল নির্লোভ এই মানুষটির। শৈশবে পিতার অকালমৃত্যুর কারণে স্কুলের গন্ডি পেরনো হয়নি। চিৎপুরে একটা মদের দোকানে বয়ের কাজ, তারপর ঘড়ি সারাইয়ের দোকানের কাজ ফেলে পালালেন রেঙ্গুনে, হলেন সার্কাসের জোকার। ভালো লাগলো না। ফিরে এসে জ্যাঠামশাইএর হাত ধরে এলেন স্টার থিয়েটারে, হলেন পাঁচ টাকা বেতনের তবলা বাদক, পরে অভিনয়ে। জীবনের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর শিবপুর থেকে সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে স্টুডিও যাতায়াতের সুবাদে নানা চরিত্রের মানুষকে পর্যবেক্ষনই ছিল তাঁর বাস্তব ঘেঁষা অভিনয়ের রসদ। বলেছেনও সে কথা “চোখ কান খোলা রাখি, আর সব ধরনের মানুষ দেখে বেড়াই। চরিত্রমতো যখন যাকে দরকার, তাকে তুলে ধরি। এ সব চরিত্র ফুটিয়ে তোলার দরকার হয় নাকি? এ সব তোমার আমার চার পাশে ঘুরছে। যে কোনো একটাকে তুলে এনে নিজের কাঁধে ভর করাও”। বাংলা সিনেমায় যেন অপরিহার্য ছিলেন তুলসী চক্রবর্তী। প্রেস কিংবা হোটেলের মালিক, গ্রাম্য টোলের মাষ্টার কিংবা গ্রামের মুদিখানার দোকানি যে চরিত্রই পেতেন তুলে আনতেন তাদের বিশ্বাসযোগ্য ছবি। অভিনয় করতেন মনেই হত না। কোন রূপসজ্জার প্রয়োজন হত না। তার সিনেমা জীবন খুব দীর্ঘ ছিল না। মাত্র ২৮ বছরের চলচ্চিত্র জীবনে অভিনয় করেছিলেন ৩১৬টি বাংলা ও ২৩টি হিন্দি ছবিতে। সিনেমা জগতের উজ্বলতার মধ্যে থেকেও আর একটু সাচ্ছন্দের লোভ তাঁকে ছুঁতে পারেনি । লোভি ছিলেন না, ছিলেন না বলেই ছিলেন অবহেলিত। পরিচালকের ডাক পেলে চলে আসতেন, পেতেন দৈনিক ২৫ কি ৩০টাকা । শুধুমাত্র সত্যজিৎ রায়ের ‘পরশ পাথর’এ দৈনিক ১৫০০ টাকা দিতেন। বিদেশের কোন শিল্পীর অনুকরণ নয়, তাঁর অভিনয় ছিল নিতান্তই দেশজ, দেশের মানুষের চরিত্রের মধ্যেই আছে সে অভিনয়ের শেকড়। পর্দায় দু তিন মিনিটের উপস্থিতি থাকতো তাঁর (ব্যতিক্রম ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ও ‘পরশ পাথর’)। সেই স্বল্প উপস্থিতিই দর্শকের কাছে অনাবিল আনন্দ নিয়ে আসতো। শিশুর সারল্য ভরা মুখ আর চোখের খেলায় শরীর নাচিয়ে এক অদ্ভুত অভিনয় ধারায় দর্শকদের মাতাতেন তুলসী চক্রবর্তী। সত্যজিৎ রায় ১৯৫৮তে যদি এই অসামান্য অভিনেতাকে মুখ্য চরিত্রে নিয়ে ‘পরশ পাথর’ না বানাতেন তাহলে বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ অপরাধী হয়ে থাকতো। সত্যজিৎ রায় স্বীকার করে গিয়েছেন যে, তুলসী চক্রবর্তী না থাকলে তিনি পরশ পাথর গল্পটি চলচ্চিত্রায়িত করতেন না। এবং এই মন্তব্যও করেছেন যে তুলসী চক্রবর্তী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে থাকলে তাঁকে অভিনয় দক্ষতার জন্য অস্কার পুরস্কার প্রদান করা হত।
তুলসী চক্রবর্তী, ভানু, জহর, নৃপতি, হরিধন, অনুপকুমার, রবি ঘোষ, সন্তোষ দত্তরা নেই। বাংলা সিনেমা থেকে কমেডি অভিনয়ও উধাও হয়ে গেছে, আছে শুধু স্মৃতি আর ইতিহাস। সেই স্মৃতি আর বাংলা চলচ্চিত্রের একশো বছরের ইতিহাস ঘেঁটে বাংলা সিনেমায় কমেডি অভিনয়ের ধারাটিকে ছুঁয়ে গেলাম।
তথ্যসূত্র –
‘সোনার দাগ’/গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ
(২) ‘অগ্রপথিকেরা’/সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
(৩) গণশক্তি/ শারদ সংখ্যা ১৪২৩
কথাসাহিত্যিক ও সম্পাদক