অবধী কামমোহিতম্
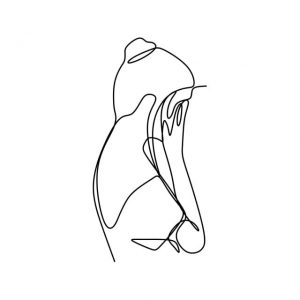 “মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকম্ অবধী কামমোহিতম্।।”
সেই পুরনো শ্লোকটা! সেই ভয়ঙ্কর শ্লোকটা! এতদিন পরে আবার সেটা দেখে মাথার মধ্যে যেন একটা সাইক্লোন চলে গেল। সেইসঙ্গে অস্বস্তি। কী যেন একটা মনে পড়বো পড়বো করেও মনে পড়ছে না।
এসেছিলাম আমার তরুণ সহকর্মী গৌতম সরখেলের বাড়িত। অনেকদিন ধরেই ডিনারটা পাওনা ছিল। ড্রয়িংরুমে ঢুকতেই চুম্বকের মতো চোখদুটো টেনে নিল দেয়ালের গায়ে লটকানো লম্বা রেক্ট্যাঙ্গুলার ফ্রেমে বাঁধানো এই শ্লোকটা। জিনিষটা বেশ অনেকদিনের পুরনো হলেও ভেতরের লেখাগুলো পড়া যায়। আর ঐ লেখাগুলোই আমাকে কী যেন মনে পড়াবার চেষ্টা করছে। অনেক চেষ্টা করেও তখন আর কিছুই মনে পড়ল না। শুধু মনের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধে রইল।
ডিনারের পর মৌজ করে বারান্দায় বসলাম গল্প করতে। রাত বেশি হয়নি। সবে দশটা। সাড়ে দশটায় উঠলেও এগারোটার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যাব। সুতরাং নিশ্চিন্তে বসলাম আড্ডা মারতে। সবে আরাম করে সিগারেটটা ধরিয়েছি। অমনি ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো মাথা। আমি সোজা হয়ে বসলাম। ঘটনাটা আমার মনে পড়ে গেছে ভালোভাবেই।
তখন আমি ফরাক্কায় পোস্টেড। আমার কাজের এলাকা ছিল ব্যারেজের কাছে আধা শহরটা। বর্ডার এরিয়া। এমনিতেই সবসময় অশান্তি লেগে থাকে, তার ওপর তখন দিনকালও ছিল উত্তাল। ফলে ওখানে তার প্রভাবও ছিল একটু বেশি। এই একদিকে পাচার চক্র, তো অন্যদিকে দাঙ্গা। কখনো কোন বস্তিতে খুনজখম, তো কোন হোটেলে স্মাগলিং বা মধুচক্রের র্যাকেট।
আমি তখন নতুন এসেছি, অতএব কাজ দেখাতে হলে একটু বেশি পরিশ্রম তো করতেই হবে। দিন নেই, রাত নেই, কোন খবর এলেই জীপভর্তি কনস্টেবল নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। ভয়ডর কিছু ছিল না। কাজও হচ্ছিলো পুরোদমে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুব একটা কমাতে পারিনি বটে, তবে স্মাগলিং চক্রের দু-চারটে মাথাকে ধরে ফেলতে ঐ ব্যাপারটা বেশ খানিকটা কমে গিয়েছিল।
ঠিক সেইরকম সময়েই ব্যাপারটা ঘটলো। এমন একটা উত্তেজনাময় ঘটনার ঢেউ এসে ধাক্কা মারলো ফরাক্কায়, যার জেরে সাময়িকভাবে গোটা ফরাক্কা তোলপাড় হয়ে উঠলো। আর সেই ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে আমিও যেন …
থাক। ব্যাপারটা প্রথম থেকেই শুরু করি।
তখন নভেম্বরের শেষ। হিমেল হাওয়া ছোবল মারতে শুরু করেছে। ভোরের শিশিরে গাছের পাতাগুলো রোজই ভিজে ওঠে। সেরকমই এক সকালে ব্রেকফার্স্ট সেরে থানার বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে খবরের কাগজটায় চোখ বোলাচ্ছি, রহমৎ এসে জানাল আমার ফোন এসেছে।
এইরকম সময়ে ফোন তো একমাত্র সুখদেও ছাড়া কেউ করবে না! সুখদেও সিং। আমার ইনফর্মার। ওর ক্রমাগত সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে এখানে কাজ করা একরকম অসম্ভবই হয়ে দাঁড়াত।
জলদি উঠে গিয়ে ফোনটা ধরি। আমার অনুমান একদম ঠিক। সুখদেও। সাধারণত খুব ঠান্ডা গলায় অল্প দু-চার কথায় যা জানাবার জানিয়ে দিয়ে ফোন রেখে দেয় সুখদেও। কিন্তু আজ দেখলাম ওর গলায় রীতিমতো উত্তেজনার সুর। কাঁপা কাঁপা গলায় ও যা বলল, শুনে আমারই ধাত ছেড়ে যাবার উপক্রম। রহিম খুন হয়ে গেছে। ওর বডিটা পড়ে আছে ব্যারেজের কাছে, খালপাড়ের নিচু জমিতে, গলাটা দা দিয়ে কোপানো।
ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। রহিমও খুন হয়ে গেল? মাত্র দু-মাস আগেই খুন হয়েছে শামসুদ, ওরই রাইভ্যাল, আর সেই খুনের পেছনে রহিমই ছিল বলে আমাদের পুলিশমহলের ধারণা। যদিও হাতেনাতে প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়নি বলে রহিমকে অ্যারেস্ট করা হয়নি, তবে তার ওপরে নজর আমাদের ছিলই। তা সত্ত্বেও এটা ঘটল। কিন্তু ঘটল কীকরে? আর ঘটালোই বা কে? শামসুদের দলেরই কেউ? তাছাড়া তো কেউ হতেই পারে না।
এস. আই. নীলেশকে খবরটা জানিয়ে চটপট আসতে বললাম। বেরোতে হবে। ড্রেস-আপ করতে করতে মনে পড়ছিল সব কথাগুলো। রহিম আর শামসুদ, এখানকার পাচারচক্রের সবচেয়ে বড়ো দুই পান্ডা। ওদের দলও বেশ বড়ো। কিন্তু আশ্চর্য, দুটো দলেরই ছুটকোছাটকা কয়েকজনকে পাকড়াও করলেও ওদের ছুঁতে পারিনি একবারের জন্যেও। অথচ মুখোমুখি দেখা হয়েছে বেশ কয়েকবার, মাঝেমধ্যে দুজনেই থানায় এসে সেলাম বাজিয়েও গেছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।
শামসুদের বাড়ি ছিল আমার এলাকার বাইরে, গঙ্গার ওপারে সুলতানগঞ্জে। কিন্তু কাজকর্ম আমার এলাকা জুড়েই। খুনও সে হয়েছিল আমার এলাকাতেই। সম্ভবত বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসে ঐ ব্যারেজের কাছেই মার্ডার করা হয় তাকে। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল তার দেহ। আর সেই দেহটা ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন। একটা সুতোও ছিল না তার শরীরে।
খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার ঘাড়েই কেসটা পড়েছিল। পিস্তলটা পেয়েছিলাম, কিন্তু তাতে কোন হাতের ছাপ ছিল না, আর পিস্তলটাও বেআইনী। ফলে কাউকেই ধরা গেল না। শুধু শামসুদের চেলাচামুন্ডাদের কাছে জানতে পেরেছিলাম, এটা রহিম আর তার দলেরই কাজ। কিন্তু কী করবো? আমার হাত-পা তো বাঁধা।
অগত্যা আমার লোকেদের বলেছিলাম রহিমের ওপর কড়া নজর রাখতে। ওরা নজরও রাখছিল, কিন্তু কী থেকে যে কী হয়ে গেল!
ফটো-টটো তুলে, বডি পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে থানায় ফিরতে ফিরতে বেলা দুটো। কোনক্রমে নাকেমুখে একটু গুঁজে বসলাম রিপোর্ট লিখতে। মিডিয়া তৎপর হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গেই শুরু হয়ে গেছে ওপরওলাদের হুমকি।
ভীষণ অসহায় লাগছিল, আর ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছিলাম। মনে হচ্ছিল, যা হয় হবে, আজ শালা ওই শামসুদ আর রহিম,ওদের দুটো দলেরই শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলবো। ঠেকগুলো মোটামুটি জানাই আছে, সবক’টাকে টেনে এনে খাঁচায় পুরবো, তারপর একটা একটা করে বেছে বেছে আড়ং ধোলাই। দেখি ব্যাটারা মুখ খোলে কী না। এমন দশা করব ওদের, যা দেখে শুধু ওরা কেন, গোটা ফরাক্কা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যাবে।
সেইমতোই ব্যবস্থা করলাম। থানার অফিসার আর কন্স্টেবলদের ডেকে একটা মিটিং, আর্ম্স রেডি করা, আর কোনদিক থেকে কীভাবে জালটা ফেলা হবে তার একটা ছোট্ট প্ল্যানিং। সম্ভবত আজ রাতে আর ঘুমই হবে না, কারণ সন্ধে সাতটার পরে আমরা শিকারে বেরবো, আর ফিরবো কখন তা কেউই জানি না।
অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটলো ঠিক সন্ধের মুখে। থানায় তখন প্রায় কেউই নেই, সকলকে একটু রেস্ট নিয়ে সাতটার মধ্যে রেডি হয়ে আসতে বলেছি, আমি নিজেও রিল্যাক্সড্ মুডে ছিলাম। এমন সময় একটা ভাঁজকরা কাগজ এনে রহমৎ আমার হাতে দিল। আমার নাম করে নাকি একটা ছেলে এসে দিয়ে গেল এইমাত্র।
অবাক হয়ে কাগজটা ভাঁজ খুলে দেখলাম। একটা চিঠি। পরিচ্ছন্ন গোটা গোটা হাতের লেখায় একটা ছোট্ট দু-লাইনের চিঠি —
‘সাহেব, রাত ঠিক আটটার সময় তিলডাঙা মসজিদের পেছনে আসবেন।
একদম একা। কারণটা এলেই বুঝবেন।’
কোন নাম নেই। কে লিখলো চিঠিটা? আমার নাম করে দিয়ে গেছে যখন, নিশ্চয়ই আমাকেই লিখেছে। কিন্তু কে এভাবে আমায় দেখা করতে বলছে গোপনে?
পুলিশ লাইনে মাঝে মাঝেই এরকম সব বেনামী চিঠি হাতে পড়ে, যার অধিকাংশই ভুয়ো। কিন্তু এই রহস্যময় চিঠিটা যেন ঠিক সেরকম নয়। যেন চিঠিটার মধ্যে কিছু একটা সত্যি লুকিয়ে আছে। আর দেখা করার কারণ হিসেবে যদিও কিছুই লেখেনি, তবু যেন মনে হচ্ছে যে, দরকারটা তার নয়, আমারই।
কয়েক মিনিট ধরে সাত-পাঁচ ভাবার পর সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি যাব। বেশি দূর তো নয়, ঐ তো তিলডাঙা স্টেশন থেকে এক কিলোমিটারের ভেতরেই ঐ মসজিদটা। আগে দু-চারবার ওদিকে গিয়েওছি। জায়গাটা মোটামুটি জানা আছে।
থানার দুটো জীপে নীলেশের দায়িত্বে ফুল আর্মড্ ফোর্স পাঠিয়ে দিলাম আজকের অ্যাকশানে, আর আমি নিজে একটা জীপ নিয়ে রওনা হলাম তিলডাঙার দিকে। ড্রাইভার সঙ্গে থাকছে যদিও, কিন্তু মসজিদ থেকে জীপটা একটু দূরে রেখে একাই যাব মসজিদের পেছনে। দেখাই যাক না কী হয়। ভয় জিনিষটা তো কোনকালেই নেই, আর ওসব থাকলে পুলিশের চাকরি না করাই ভালো।
জায়গাটা বেশ নিঃঝুম। মসজিদটাও অনেকদিনের, বেশ পুরোনোই, আর ফাঁকা ফাঁকা। সন্ধের আজানের পরে আরও চুপচাপ হয়ে গেছে। শুধু টিমটিম করে গোটাদুয়েক ফ্যাকাশেমার্কা হলদে আলো জ্বলছে। বাইরের আকাশে যদিও চাঁদের আলো আছে, কিন্তু সে আলোয় অল্পই দেখা যায়।
নিঃসাড়ে মসজিদের পেছনে গেলাম। পেছন দিকটা বেশ অপরিষ্কার। আগাছা আর ঝোপঝাড়, দু-চারটে বড়ো বড়ো গাছ। একটা চারসেলের টর্চ সঙ্গে ছিল, সেটা জ্বেলে চারপাশে আলো ফেলছিলাম। ডানহাতটা কোমরের হোলস্টারে, সেখানে সার্ভিস গানটা আমার মনে সাহস যোগাচ্ছে।
আলোটা চারদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ একটা বড়ো গাছের পেছনে কালোমতন কিছু একটার নড়াচড়া চোখে পড়ল এক পলকের জন্য, আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা নির্দেশ ভেসে এল — ‘আলোটা নেভান।’
হতবাক হয়ে টর্চটা নিভিয়ে দিলাম। মহিলার গলা! একজন মহিলা আমাকে চিঠি দিয়ে ডেকেছেন! এরকম সম্ভাবনা তো একবারের জন্যেও আমার মনে আসেনি!
চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, আবার সেই মহিলার কথা শোনা গেল, ‘এদিকে এগিয়ে আসুন, এই গাছের পিছনে।’ এবার গলাটা একটু চাপা, আর কেন যেন মনে হল গলাটা খুব বয়স্কা কোন মহিলার নয়, খানিকটা যেন কমবয়েসী কোন তরুণীর।
অবাক হয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে গেলাম গাছের পেছনে। একটি বোরখাপরা মহিলা। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই মুখের সামনের ঢাকাটা তুলে ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বললেন, ‘আমার নাম মধুরা। আমিই আপনাকে ডেকেছিলাম। আর সেটা আপনারই প্রয়োজনে। কারণ একটা কথা আপনার জানা দরকার… ’
এক মুহূর্ত থেমে ভদ্রমহিলা স্থির গলায় বললেন, ‘আমিই রহিমকে খুন করেছি। এবার আপনি কী করতে চান বলুন।’
আমার এতদিনের পুলিশী জীবনে আমি বোধহয় এত অবাক কোনদিন হইনি। চোখধাঁধানো সুন্দরী সেই মহিলা, বয়েস খুব বেশি হলে কুড়ি থেকে বাইশের মধ্যে। কিন্তু তার আয়ত চোখদুটি থেকে যে প্রচন্ড একটা সংহত শক্তি ফুটে বেরোচ্ছে, তা আমার আঠাশ বছরের যৌবনের ভিত পর্যন্ত অক্লেশে নাড়িয়ে দিতে পারে।
গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছিল না। কোনরকমে বললাম, ‘আপনি খুন করেছেন রহিমকে? কিন্তু কেন?’
মেয়েটি একটু হাসল। সেই হাসির ঝিলিক যেন তার ডাগর চোখদুটোকেও ছুঁয়ে গেল। কিন্তু সে মাত্র এক মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই আবার ধারালো কঠিন সেই মুখ। একটা শাণিত ছুরির ফলার মতো ঝলক খেলে গেল তার চোখে, আর তার দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁটদুটো উচ্চারণ করল, ‘বেশ করেছি। শুধু খুন নয়, যদি আরও কিছু করতে পারতাম, তাহলেই বোধহয় শান্তি হত আমার। কিন্তু আরকিছু করার ক্ষমতা তো আমার নেই, তাই শুধু ওর গলাটাই কেটেছি কুপিয়ে কুপিয়ে। কী, ভালো করিনি, বলুন?’
কী বলব আমি? আমার স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি তখন উধাও। মাথার মধ্যে কিলবিল করছে একরাশ প্রশ্ন। সব মিলিয়ে যেন একটা কঠিন ধাঁধার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিলাম। অথচ আকস্মিকভাবে এই অদ্ভুত পরিস্থিতির সামনে পড়েকী করব সেটাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।
ঠিক এই সময় আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে মেয়েটি তার বোরখার ভেতর থেকে বার করে আনল একটা মাঝারি সাইজের দা। নির্দ্বিধায় আমার হাতে সেটা তুলে দিয়ে বলল, ‘এই নিন। আমার কাছে এটার দরকার ফুরিয়ে গেছে।’
অল্প চাঁদের আলোয় সেই দা-টা দেখে চমকে উঠলাম। দা-এর ধারালো অংশে কেমন কালো কালো ছোপ।
রহিমের গলার রক্ত! আমার ইস্পাতকঠিন শিরদাঁড়াও যেন হঠাৎ শিরশির করে উঠল ওটা দেখে।
মেয়েটির কিন্তু কোন তাপ-উত্তাপ নেই। বলল, ‘কী ব্যাপার! কিছু বলছেন না যে? এবার বলুন কী করতে চান?’
ততক্ষণে একটু একটু করে সাড় ফিরে এসেছে আমার শরীরে। পেশিগুলো টানটান, গোটা শরীরে আবার রক্তের চলাচল তার নিজস্ব গতিতে।
পকেট থেকে রুমাল বার করে ধীরেসুস্থে দা-টাকে মুড়ে নিই। তারপর চারপাশে তাকাতে তাকাতে গম্ভীর গলায় মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি, ‘আচ্ছা মধুরা, এখানে আশেপাশে কোন বসার জায়গা আছে?’
মধুরা একটু অবাক গলায় প্রশ্ন করে, ‘কেন বলুন তো?’
সংক্ষেপে বলি, ‘দরকার আছে।’
মধুরা একটু ইতস্তত করে। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, ‘ওপাশে একটা বটগাছের তলায় একটা বাঁশের বেঞ্চি আছে। ছেলেরা আড্ডা মারে।’
‘বেশ, ওখানেই চলো।’
দুজনে চুপচাপ এগিয়ে গেলাম সেদিকে। অল্প ঝিঁঝিঁপোকার ডাক ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। বটগাছের ঘন ডালপালার নিচে চওড়া বেঞ্চিটা অন্ধকার।
দা-টা পাশে রেখে পা ঝুলিয়ে বসলাম বেঞ্চিটায়। মধুরাও বসল একটু দূরত্ব রেখে। যদিও ওর মধ্যে কোন সংকোচ, কোন জড়তাই চোখে পড়ল না। বরং আমিই এখনও ঠিক সহজ হতে পারিনি। কিন্তু ঠিক কী করতে চাই, হয়তো নিজেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এই মেয়েটা খুনী, আর সে নিজে সেটা স্বীকার করতে এসেছে আমার কাছে, এই নির্জন জায়গায় ডেকে নিয়ে। কারণটা কী? রহিমের সঙ্গে ওর সম্বন্ধটা কী? কেনই বা সে খুন করল রহিমকে? মনের মধ্যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন এসে আছড়ে পড়ছে। কিন্তু এই অদ্ভুত আকস্মিকতার ধাক্কায় সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।
এইভাবে মিনিটখানেক কেটে যাবার পর হঠাৎ বোমার মতোই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম মধুরার দিকে, ‘রহিম তোমার কে হয় মধুরা?’
এতদিনের পুলিশি অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এইরকম হঠাৎ ধাক্কা বহু ঘাগু অপরাধীকে শুইয়ে দেয়। মনের জোর পলকে হারিয়ে ফেলে তারা। কিন্তু চমকে উঠলাম এই একচিলতে মেয়েটার মনের শক্তি দেখে। স্থির অকম্পিত গলায় মধুরা বলল, ‘সাহেব, অত ধানাই পানাই করছেন কেন?সোজা কথায় বলুন না যে, আপনি আসলে গল্পটা শুনতে চাইছেন!’
মনে মনে কুর্নিশ করি মধুরাকে। কিন্তু বাইরে তো সে ভাব দেখালে চলবে না। তাই গলাটা ঝেড়ে নিয়ে পরিষ্কার গলায় বলি, ‘হ্যাঁ তাই। প্রথম থেকে পুরো গল্পটা আমায় বলো তো! তারপর দেখি তোমায় নিয়ে কী করা যায়।’
বলে হোলস্টার থেকে সার্ভিস গানটা বার করে কোলের ওপর রাখি। এও একটা মানসিক চাপ সৃষ্টি। অপরাধীরা পুলিশি অস্ত্র দেখলে মিথ্যের আশ্রয় নিতে দুবার ভাবে। আর মধুরাকেও আমি এই মুহূর্তে অপরাধী ছাড়া কিছুই ভাবছি না।
মধুরা একবার তাকাল আমার কোলে রাখা অস্ত্রটার দিকে। একবার আমার মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল তার গল্প।
সে গল্প আবেগ মেশানো ভয়ঙ্কর এক গল্প। সে গল্প বিপদের বেড়াজালে ঘেরা এক উদ্দাম রোম্যান্সের গল্প। মধুরার সেই গল্প যেন ধীরে ধীরে আমাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলল।
মধুরার মামার বাড়ি ব্যারেজের ঠিক ওপারে। ছোটবেলাতেই ওর মা আর বাবা দুজনেই একে একে মারা যান। মধুরার জীবনযাত্রা শুরু হয় ওর মামার বাড়িতে। মামারও একটাই মেয়ে। প্রায় ওরই বয়েসী। সেই মামাতো বোনের সঙ্গেই একসঙ্গে বড় হয়ে ওঠে মধুরা। সেইসঙ্গে ক্রমশই হয়ে ওঠে সুন্দরী ও শিক্ষিতা।
শামসুদ তার কাজ কারবারের সূত্রে সুলতানগঞ্জ থেকে গঙ্গা পেরিয়ে এই এলাকায় আসত প্রায়ই। সেরকম কোন যাতায়াতের সময়েই তার চোখে পড়ে মধুরাকে। পনেরো-ষোলো বছর বয়েস তখন মধুরার। বাড়ন্ত গড়ন, সেইসঙ্গে অসামান্যা রূপ। আর শামসুদও বলিষ্ঠ যুবক। অতএব শুরু হল আশনাই। আর তা গড়াতে গড়াতে অনেকদূর। শামসুদের কাজ সম্পর্কে মধুরা যখন জানল, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ফেরবার কোন রাস্তা আর খোলা নেই।
ছোট জায়গা। খবর খুব একটা চাপা থাকে না। শামসুদ আর মধুরার ব্যাপারটাও আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল এ কান থেকে সে কান। চোখেও পড়ল অনেকের। তাতে শামসুদ নির্বিকার থাকলেও মধুরা যেন হঠাৎ আরও বেশি করে উদ্দাম আর মরীয়া হয়ে উঠল। কারণ মেয়েদের একস্ট্রা যে সেন্স থাকে, তা থেকেই মধুরা টের পাচ্ছিল, ওকে নিয়ে শামসুদের ওপর অনেকেরই ঈর্ষার মেঘ ক্রমশ ঘনিয়ে উঠছে। আর তাদের মধ্যমণি হল রহিম।
এমনিতেই পেশাগত ব্যাপারে দুজনের সম্পর্ক সাপে নেউলে। তার সঙ্গে মধুরার অস্তিত্ব যেন বারুদের স্তূপ হয়ে জমে উঠতে লাগল দিনের পর দিন। শুধু একটা স্ফূলিঙ্গের অপেক্ষা। সেই আঁচ থেকে শামসুদকে আড়াল করে রাখার জন্যেই মধুরাও যেন নিজের সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে আঁকড়ে ধরল শামসুদকে।
তবুও শেষরক্ষা হল না। স্ফূলিঙ্গটা লাগলই। একটা অসতর্ক মুহূর্তে মধুরার চোখের সামনেই শামসুদকে টেনে নিয়ে গেল ওরা। মধুরা কিছুই করতে পারেনি। চিৎকার করেছে, হাহাকার করেছে, পাগলের মত একে ওকে ডেকে সাহায্য চেয়েছে। কিন্তু কেউই ওকে সাহায্য করতে পারেনি। তারপর, পরের দিন সকালে বোবার মত চুপ করে শুনেছে শামসুদের মৃত্যু সংবাদ। অন্যরাই শুনিয়েছে। কিন্তু যারা সেই খবরটা শুনিয়ে গেছে, তারা তখন মধুরার বুকের ভেতরটাও পড়তে পারেনি। তাই মাত্র এক মাসের মধ্যেই মধুরাকে দেখে অবাক হয়ে গেছে সবাই।
রহিম এসে মধুরার সঙ্গে দেখা করেছিল শামসুদ মারা যাবার এক সপ্তাহ পরেই। আর, শুধু চোখের মিনতি নয়, লুচ্চা ভাষায় একদম খোলা গলাতেই জানিয়েছিল যে মধুরাকে তার চাই। তারপর এক মাসের মধ্যেই রহিমের সঙ্গে মধুরাকে দেখা যেতে লাগল প্রায়ই। এধারে, ওধারে, নির্জনে, কিংবা মাঝেমধ্যে লোকের চোখের সামনেও।
‘তারপর? তারপর?’ আমার গলা থেকে ব্যগ্র স্বর বেরিয়ে আসে। মধুরা গল্প বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেছে। কিন্তু সে গল্পে আমি এমনই ইন্ভল্ভড হয়ে গিয়েছিলাম যে স্থান কাল ভুলেই বসেছিলাম। এখন নিজের কন্ঠস্বরেই যেন চমক লাগে। কিন্তু আগ্রহটা দমন করতে পারি না। আবার জিজ্ঞেস করি মধুরাকে, ‘তারপর কী হল মধুরা?’
চোখে পড়ে মধুরা অন্যমনস্ক। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে চুপ করে। আমি সময় দিই ওকে। নিস্তব্ধ দু এক মিনিট পার করে আবার মুখ খোলে মধুরা, ‘মামার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল আমায়। রহিমই চেনা একটা লোকের বাড়ি ঠিক করে দিল। একটা ঘরে কোনক্রমে থাকার ব্যবস্থা হল। সবে তো একমাস হয়েছে, সে ভাড়াটা রহিমই দিয়েছে। কিন্তু আর তো সেখানে আমার ফেরা হবে না।’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মধুরা।
এ সব আজেবাজে কথা শোনার সময় আমার নেই। আমার চাই গল্পের শেষ । তাই বেশ কঠিন গলায় বললাম, ‘ওসব কথা রেখে আসল কথাটা বলো মধুরা। এর পর কী ঘটলো? সব কিছুই তো ঠিক হয়ে গেল। তাহলে এর পরেও কেন রহিমকে খুন করতে হল?’
মধুরা এবার পূর্ণদৃষ্টিতে ফিরে তাকায় আমার দিকে। ওর চোখে শ্লেষ মাখানো হাসি।
‘এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি পুলিশে চাকরি করছেন? এ তো পাড়ার লোকের কথা। ঐ যে, যারা রহিমের সঙ্গে আমায় ঘুরতে দেখে আমার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করত! যারা জানে না ভালবাসা কাকে বলে! যারা ভাবতেও পারে না, একটা মেয়ে ভালবাসলে কী করতে পারে!’
বাকরুদ্ধ হয়ে যাই। এতক্ষণে মধুরার আসল উদ্দেশ্য আমার চোখে ধরা পড়ে যায়।
‘তার মানে… তার মানে…! কিন্তু এই তীব্র ঘৃণা কেন মধুরা? যেভাবে কোপের পর কোপ চালিয়েছো ওর গলায়, তাতে মনে হয়, তীব্র এক প্রতিশোধের স্পৃহায় কোন উন্মাদিনী যেন!
আমাকে কথা শেষ করতে দেয় না মধুরা। তার আগেই বলে ওঠে, ‘হ্যাঁ প্রতিশোধ। বাল্মিকীর প্রতিশোধ। সেই ব্যাধটাকে মেরেছি আমি। এতে অন্যায় তো কিছু নেই!’
অবাক হয়ে বলি, ‘বাল্মিকীর প্রতিশোধ? মানে?’
মধুরা আবার হাসে। তারপর বলে, ‘দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মিকী হয়ে ওঠার সেই প্রথম স্টেজটা জানেন না? মিলনরত এক ক্রৌঞ্চ দম্পতিকে একটা ব্যাধ তীর ছুঁড়ে মেরেছিল। আর সেই দৃশ্য দেখেই বাল্মিকীর কন্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছিল তাঁর প্রথম শ্লোক — ‘মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকম্ অবধী কামমোহিতম্।।’’
স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকি। না, মধুরার মুখে এই বিশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক শুনে নয়, ওর এই শেষ কথাটায় মধুরা যেন আমার চোখের সামনে থেকে সমস্ত রহস্যের পর্দা টান মেরে খুলে দেয়। মনে পড়ে যায় শামসুদের নগ্ন দেহটার কথা। উত্তেজিত হয়ে বলে উঠি, ‘তার মানে তোমরা কি তখন! মানে তোমাদের সেই অবস্থা থেকেই ওরা শামসুদকে?
মধুরা বলে, ‘সেই ব্যাধটা এখনও ফিরে ফিরে আসে, জানেন তো? অন্য রূপে, অন্য চেহারায়। তাদেরই একজনকে আমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছি চিরদিনের মতো। এর জন্যে আইন কী বলবে জানি না, কিন্তু আমার কোন অপরাধবোধ নেই।’
এরপর বহুক্ষণ কেটে গেছে। চুপচাপ বসে ছিলাম সেই বেঞ্চে। থমথমে অন্ধকার আমার চারপাশে আরও ঘনিয়ে এসেছে। শুধু গাছের ফাঁক দিয়ে ভেসে আসা চাঁদের আলোটা যেন আরও উজ্জ্বল।এবার উঠতে হবে। যাবার সময় দা-টা কোথাও পুঁতে রেখে যাব, যাতে রহিমের খুনের কেসটা সেখানেই ক্লোজ্ড হয়ে যায়।
মধুরা অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে। আমিই ওকে যেতে দিয়েছি। শুধু যাবার আগে জানতে চেয়েছিলাম, ‘চলে যেতে চাইছো কেন? এখানেই কোথাও থেকে যাও না। আমি না হয় ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আর অজানা অচেনা জায়গা। তোমার সঙ্গেই বা থাকবে কে?’
ঠিক সেইরকম হেসে মধুরা বলেছিল, ‘ভয় পাবেন না সাহেব, শামসুদ আমার সঙ্গে থাকবে। আর ওকে বাঁচানোর জন্যেই আমাকে চলে যেতে হবে।’ এই বলে ওর নিজের পেটটায় আলতো করে একবার হাত ছুঁইয়েছিল, তারপর ধীর পায়ে মিলিয়ে গিয়েছিল অন্ধকারে।
কথাসাহিত্যিক
জন্ম ১৯৬৪। পেশায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। অথচ শিল্প, সাহিত্য আর সংস্কৃতি নিয়েই তাঁর বেঁচে থাকা। তাই অসংখ্য ছোটবড় পত্রিকায় তাঁর বিভিন্ন ধরণের লেখা প্রকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়ে চলা নাটক ও নৃত্যনাট্য রচনা ও সুরারোপের মাধ্যমেও বিচ্ছুরিত তাঁর প্রতিভা। লেখেন ছোটবড় সকলের জন্যই। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১১, যার মধ্যে ‘দুর্দান্ত দশ’, ‘পাতায় পাতায় ভয়’, ‘ভূতের বৃন্দাবন’, ‘গুহা গোখরো গুপ্তধন’ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি ইতোমধ্যেই পাঠকসমাজের কাছে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর রচিত ও সুরারোপিত অপেরা-নাটক “আলাদিন” বেশ কয়েকবার মঞ্চস্থ হওয়া ছাড়াও হাওড়ার একটি নাট্য কর্মশালায় ব্যবহৃত হয়েছে। একসময় সম্পাদনা করেছেন সাহিত্য পত্রিকা “আলো অন্ধকার”। পেয়েছেন কয়েকটি পুরস্কার, যার মধ্যে ‘কিশোর ভারতী সাহিত্য পুরস্কার”, “সংশপ্তক পুরস্কার” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।